সিলেটের ‘হাইস্কুল’র ইতিকথা
প্রকাশিত হয়েছে : ৪:০৯:৩০,অপরাহ্ন ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ | সংবাদটি ৩৮৩ বার পঠিত
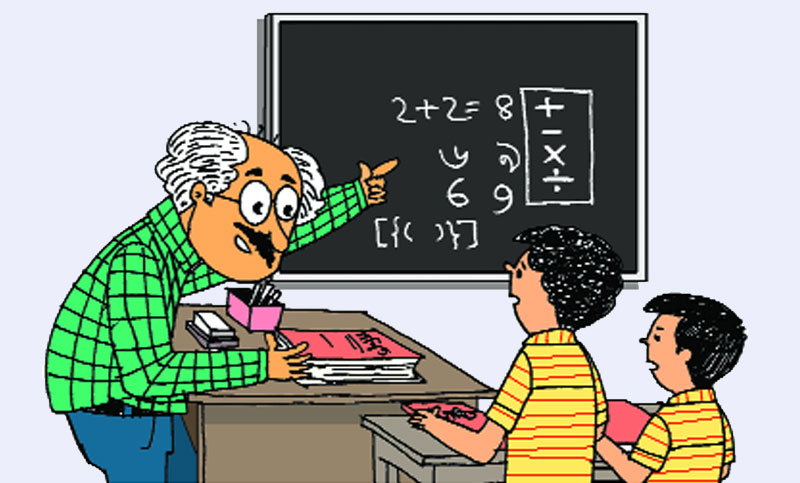 আমাদের প্রতিদিন ডেস্ক:: ১৮৩৫ সালে লর্ড মেকোলি একটি শিক্ষা কাঠামো প্রণয়ন করেছিলেন। ১৮৩৫-৩৮ সালে সরকারের শিক্ষা-বিষয়ক সার্ভেয়ার উইলিয়াম অ্যাডামের সার্ভে ও সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিটি জেলা শহরে একটি করে জেলা স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ১৮৩৫-৪১ সালের মধ্যে সরকারি অর্থায়নে স্থানীয় ভাষায় শিক্ষা সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করা হয়।
আমাদের প্রতিদিন ডেস্ক:: ১৮৩৫ সালে লর্ড মেকোলি একটি শিক্ষা কাঠামো প্রণয়ন করেছিলেন। ১৮৩৫-৩৮ সালে সরকারের শিক্ষা-বিষয়ক সার্ভেয়ার উইলিয়াম অ্যাডামের সার্ভে ও সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিটি জেলা শহরে একটি করে জেলা স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ১৮৩৫-৪১ সালের মধ্যে সরকারি অর্থায়নে স্থানীয় ভাষায় শিক্ষা সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করা হয়।
উল্লিখিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ১৮৪০ সালের এপ্রিলে ৭৬ জন ছাত্র নিয়ে ‘সিলেট প্রবেশনাল স্কুল’ নামে একটি স্কুল চালু হয়। প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন মি. ওয়াটসন। স্কুলটির প্রথম ছাত্রদের মধ্যে একজন খ্রিষ্টান, দুজন মুসলমান ছিল। বাকি ৭৩ জনই ছিল হিন্দু। স্কুল পরিচালনা বাবদ সরকারের খরচ দেখানো হয় ৩৬ টাকা ৫ আনা ১০ পয়সা (৩৬৪)। স্কুলটি তখন স্থানীয়দের কাছে ‘বাবু স্কুল’ নামেই পরিচিত ছিল।
১৮৪১ সালে স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার-সম্প্রসারণের মতো আগের ব্যাপক নীতিমালাকে বাতিল করে সরকার কেবল ইংরেজি শিক্ষার দিকে মনোযোগ দেয়। এই পরিবর্তিত নীতিমালার ভিত্তিতে ১৮৪১ সালে ঢাকা গভর্নমেন্ট স্কুলের সঙ্গে একটি কলেজ শাখা যুক্ত হয়। এই কলেজ শাখার অধীনে সিলেট প্রবেশনাল স্কুলটি ‘সিলেট স্কুল’ নাম ধারণ করে। সে বছরের ২ জানুয়ারি সিলেট স্কুলের পণ্ডিত নিয়োগ দেওয়া হয় গৌরীশঙ্কর তর্কালঙ্কারকে। এর পরের বছর ছাত্রসংখ্যা বেড়ে ১৫১ জনে উন্নীত হয়। এর মধ্যে চারজন খ্রিষ্টান, ১২৭ জন হিন্দু ও ২০ জন ছিল মুসলমান। গড়পড়তা উপস্থিতির হার ছিল ৬ এবং মাসিক খরচ ৩৬ টাকা ৫ আনা ১০ পয়সা। একই বছর স্কুলটি ২,৬০০ টাকা সরকারি অনুদান পায়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে ১৮৪৩ সালে ছাত্রসংখ্যা ৬২ জনে নেমে আসে।
১৮৪৫ সালে স্কুল পরিচালনা কমিটিতে ছিলেন এইচ সেইনফোর্থ (জজ), এ এস আনন্দ (অ্যাকটিং কালেক্টর), ই এস পিয়ারসন (সেক্রেটারি, অ্যাসিস্ট্যান্ট টু দ্য ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড কালেক্টর), এইচ জে থ্রনটন (সিভিল সার্জন), সৈয়দ আব্বাস আলী খান (প্রিন্সিপাল সদর আমিন) ও সৈয়দ বখত মজুমদার (জমিদার)। শিক্ষকমণ্ডলীতে ছিলেন প্রধান শিক্ষক জে কেলসো, দ্বিতীয় মাস্টার জি সুইনি ও পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কালঙ্কার। সে বছর বার্ষিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের ফলাফল সন্তোষজনক ছিল না। স্কুলের দুজন ছাত্র জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় অংশ নিলেও তারা ভালো ফল করতে পারেনি। কমিটি এ জন্য প্রধান শিক্ষককে দায়ী করে। পরিণামে প্রধান শিক্ষক পদত্যাগ করলে মি. আর হ্যান্ডকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনিও চার মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই অসুস্থতার কারণে পদত্যাগ করেন। একই সময়ে সেকেন্ড মাস্টার জি সুইনিও পদত্যাগ করলে স্কুলটি শিক্ষকের অভাবে সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। পরে ঢাকা কলেজের সিনিয়র বিভাগের চতুর্থ মাস্টার জে ডব্লিউ ওয়াটসনকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে স্কুলটি আবার চালু করা হয়। শিক্ষকদের নিয়োগ ও পদত্যাগ ইত্যাদির কারণে ১৮৪৫ সালে স্কুলে কোনো পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। দ্বিতীয় মাস্টার জি সুইনির পদত্যাগের পর তাঁর পদটি খালি ছিল। ১৮৪৬ সালের ৮ এপ্রিল তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন বাবু কেশবচন্দ্র ঘোষ এবং ১৮৪৭ সালের ৯ জুন তৃতীয় মাস্টার হিসেবে কেষ্ট সুন্দর ঘোষ যোগ দেন।
১৮৪৭-৪৮ সালে শিক্ষাবর্ষের প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৮৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিলেটের নবীগঞ্জ ও জৈন্তাপুরে দুটি স্কুল চালু করা হয়। নবীগঞ্জ স্কুলে ছাত্র ছিল ৩২ জন এবং জৈন্তাপুরে ১৭ জন। ছাতক স্কুল সম্পর্কে বলা হয়, স্কুলটির কথা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, ওই স্কুল মাত্র কয়েক মাস টিকেছিল। তার বদলে লস্করপুরে স্কুল চালুর প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিবেদনটি লেখা পর্যন্ত কালেক্টর স্কুলঘর তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারেননি বলে উল্লেখ করা হয় প্রতিবেদনে।
এর মধ্যে ওয়াটসন বাঙ্কোরায় বদলি হয়ে গেলে ১৮৪৮ সালে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পদে পান টি জি মাইলস। সে বছরের ৩০ এপ্রিল গঠিত স্কুলের পরিচালনা কমিটির কর্মকর্তা ছিলেন এইচ স্টেইনফোর্থ (জজ), এ এস আনন্দ (কালেক্টর), বি এইচ কুপার (অ্যাকটিং ম্যাজিস্ট্রেট), ডি জে ওকালাগহান (সিভিল অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন) ও সৈয়দ বখত মজুমদার (জমিদার)। প্রধান শিক্ষক ছিলেন টি জি মাইলস, সেকেন্ড মাস্টার কেশবচন্দ্র ঘোষ, থার্ড মাস্টার কেষ্টচন্দ্র ঘোষ ও পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তর্কালঙ্কার।
১৮৪৯ সালে স্বাস্থ্যগত কারণে টি জি মাইলস বদলি হয়ে যান। ১৮৫০ সালের ১৩ মার্চ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন উইলিয়াম হেনরি ফক্স। তখন সেকেন্ড মাস্টার কেশবচন্দ্র ঘোষ চলে গেলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন কেষ্ট সুন্দর ঘোষ। সে বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর স্কুল পরিচালনা পর্ষদে আবারও পরিবর্তন আসে। তখন কমিটিতে আসেন এফ স্কিপউইথ (জজ), এম শো (অফিশিয়েটিং কালেক্টর), উইলিয়াম বি বাকল (ম্যাজিস্ট্রেট), সি জি অ্যান্ডুজ (সিভিল অ্যাসিসট্যান্ট সার্জন), টি পি লারকিন্স (অ্যাসিস্ট্যান্ট টু দ্য কালেক্টর অ্যান্ড মেজিস্ট্রেট), সৈয়দ বখত মজুমদার (জমিদার), মৌলভি সাদত আলী খান (সদর আমীন) ও রামগতি মিত্র (ডেপুটি কালেক্টর)। স্কুলের পরীক্ষক ছিলেন রেভারেন্ড উইলিয়াম প্রাইজ, এফ স্কিপউইথ, টি পি রলারকিন্স, রামগতি মিত্র ও দ্বারকানাথ ব্যানার্জি। তাঁদের মধ্যে টি পি লারকিন্স তাঁর চাকরির পাশাপাশি স্কুলের ইংরেজির হেড মাস্টারও ছিলেন। ১৮৫০ সালে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ৫২ জনে নেমে আসে। তবে ১৮৫১ সালে এ সংখ্যা ১১৪ জনে উন্নীত হয়। স্কুলের কালিকুমার গুহ, গোবিন্দপ্রসাদ চক্রবতী, কালনাথ কর ও রাজকুমার মিত্র জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ও প্রথম শ্রেণির ছাত্র গোবিন্দপ্রসাদ চক্রবর্তী জুনিয়র বৃত্তি পায়। এ ছাড়া আরও তিন ছাত্র সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা পাস করে।
১৮৫৪ সালে এই স্কুলে ১৯ জন মুসলমান ও ১১৫ জন হিন্দু ছাত্র ছিল। স্কুল কমিটি মুসলমান ছাত্র কম হওয়ার কারণ হিসেবে আরবি ও ফার্সি শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকার কথা বললেও ‘জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন’ এর প্রতিকার করতে সম্মত হয়নি।
১৮৫৬ সালে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান উমাচরণ দাস। অন্য শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন এম ডিয়াস, রামমোহন দত্ত, বৈদ্যনাথ দেব ও শ্যামচরণ সরকার। সে বছর স্কুলের চারজন ছাত্র জুনিয়র বৃত্তি পাস করে ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়।
রবিনসনের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে স্কুলটিতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৭৫ জন, যা পরে ১৭৯ জনে উন্নীত হয়। এর মধ্যে মাত্র তিনজন ছিল মুসলমান। কিন্তু সে বছর সিপাহি-বিদ্রোহের সময় জেলা স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়।
১৮৪৭-৪৮ সালে শিক্ষাবর্ষের প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৮৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিলেটের নবীগঞ্জ ও জৈন্তাপুরে দুটি স্কুল চালু করা হয়। নবীগঞ্জ স্কুলে ছাত্র ছিল ৩২ জন এবং জৈন্তাপুরে ১৭ জন। ছাতক স্কুল সম্পর্কে বলা হয়, স্কুলটির কথা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, ওই স্কুল মাত্র কয়েক মাস টিকেছিল। তার বদলে লস্করপুরে স্কুল চালুর প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিবেদনটি লেখা পর্যন্ত কালেক্টর স্কুলঘর তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারেননি বলে উল্লেখ করা হয় প্রতিবেদনে। এ ছাড়া ফরিদপুরের স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সিলেটে চতুর্থ আরেকটি স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব থাকলেও এর স্থান এখনো নির্ধারণ করা হয়নি বলেও উল্লেখ করা হয়।
(প্রকাশের অপেক্ষায় থাকা লেখকের ‘সিলেটের ইতিহাস: ব্রিটিশ আমল’ গ্রন্থ থেকে) সূত্র: প্রথমআলো।






